সিপিডির মূল্যায়ন
১৫ বছরে ব্যাংক থেকে ৯২২৬১ কোটি টাকা লুট
নিজস্ব প্রতিবেদক | প্রকাশিত: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৪:০৪
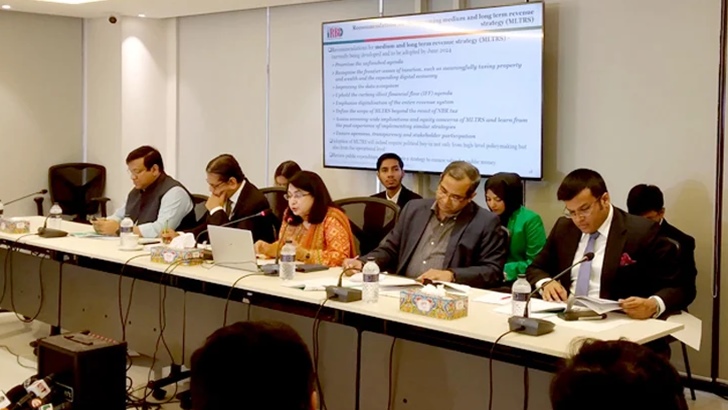
বড় ধরনের চাপে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি। এর আগে একসঙ্গে এত চ্যালেঞ্জ কখনো আসেনি। অর্থনীতি ক্রমেই ভঙ্গুর থেকে ভঙ্গুরতর হচ্ছে। ২০০৮ থেকে ২০২৩ সাল-১৫ বছরে দেশের ব্যাংকিং খাত থেকে ৯২ হাজার ২৬১ কোটি টাকা লুট করেছে ২৪টি প্রতিষ্ঠান। এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে ৩টি পদ্মা সেতু করা সম্ভব। এছাড়াও ৫ বছরে জিনিসপত্রের দাম ৯ শতাংশ থেকে শুরু করে ৪০০ শতাংশ বেড়েছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মূল্যায়নে এসব বিষয় উঠে এসেছে।
শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজস্ব কার্যালয়ে ‘দেশের অর্থনীতির চলমান সংকট ও করণীয়’ নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলা হয়। সংস্থাটির মতে, শ্রম ইস্যুতে সংস্কার বা কার্যকর উদ্যোগ না হলে বৈদেশিক বাণিজ্য ও রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, গবেষণা পরিচালক ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, সিনিয়র রিসার্স ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ। তাদের মতে, অর্থনীতির সংকট সমাধানে বড় ধরনের সংস্কার দরকার। এক্ষেত্রে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা জরুরি। কিন্তু দেশ যে ধরনের নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে, তাতে সংস্কারের আশা দেখা যাচ্ছে না। ফলে আগামী দিনে সংকট আরও বাড়বে। এছাড়াও সুদের হার ও মুদ্রা বিনিময় হার পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে।
ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, অর্থনীতি ক্রমশ ভঙ্গুর থেকে ভঙ্গুরতর হচ্ছে। ব্যাংকিং খাত বৈকল্য দশায় পড়েছে। মূল্যস্ফীতির পাগলা ঘোড়া চলা অব্যাহত রয়েছে। বৈদেশিক খাত পঙ্গু অবস্থা এবং শ্রম খাতে অন্ধত্ব বা স্থবিরতা বিরাজ করছে। তিনি বলেন, দেশের এক-তৃতীয়াংশ পরিবার রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বৈধ পথে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছে, অবৈধভাবে তা অনেক আসছে। এক থেকে দুই বছর আগে একটি সংস্থার হিসাবে দেখানো হয়েছে, অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ রেমিট্যান্স আসছে। এখন সেটি আরও বৃদ্ধির কথা। এর মানে হলো, মানুষের হাতে এখনো কিছুটা অর্থ আছে। তবে তাদের সঞ্চয় কমছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শ্রম ও মানবাধিকারের জায়গায় তিন ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অর্থনীতির জায়গায় সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। শ্রম অধিকারে সহযোগিতা স্থবির এবং মানবাধিকার বা রাজনীতির জায়গাটিতে অবনমন হচ্ছে।
এ ধরনের শক্তির আন্তঃক্রিয়ার ভেতরে দেশের অর্থনীতি এগোচ্ছে। এ পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ১২টি প্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের সংস্কার জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), প্রতিযোগিতা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেপজা), শ্রম আদালত, শিল্প পুলিশ, ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে এ ধরনের কোনো সংস্কারের আশা দেখছি না। কারণ, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হলে সাধারণত এ ধরনের বড় সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার তৈরি হয়। সে ধরনের নির্বাচনের দিকে দেশ যাচ্ছে না, সেরকম একটি ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। ফলে বর্তমানে যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সেটি আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
ফাহমিদা খাতুন বলেন, বেশ কয়েকটি খাতে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি চাপে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব আহরণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকে তারল্য সংকট, মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য কমে যাওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুত কমে যাওয়া। তিনি বলেন, মোটা দাগে ৫টি বিষয় আলোচনা করে সিপিডি। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি রাজস্ব পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকিং খাত, বৈদেশিক খাত ও ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শ্রম অধিকার। তার মতে, রাজস্ব আদায় কমছে। আমদানি কমায় কমছে পরোক্ষ কর। ফলে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলছে, রাজস্ব আয়ে ৫৫ হাজার কোটি টাকার মতো ঘাটতি থাকবে না। ফলে ধারণা করছি, জাতীয় বাজেটের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হবে।
তার মতে, সরকারি ব্যয় আরও না কমালে প্রাথমিক ব্যালেন্সে ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে না। কারণ, বিভিন্ন সংস্কারের কাজ এখনো অসম্পূর্ণ। কর আদায়ের নতুন কোনো ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। কিন্তু সম্পদ কর এবং ডিজিটাল অর্থনীতি বাড়িয়ে কর আদায় বাড়ানো সম্ভব ছিল। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বাইরেও (এনবিআর) রাজস্ব আদায় বাড়ানো সম্ভব। আর মূল্যস্ফীতি পুরোটাই আমদানিকৃত। ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, গত ৫ বছরে জিনিসপত্রের দাম বেসামালভাবে বেড়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের দাম ৯ শতাংশ থেকে শুরু করে ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রসুনের দাম বেড়েছে ৪০০, পেঁয়াজ ৩৩৩, চিনি ১৭৭, শুকনা মরিচ ১২৩, আদা ১১৮, পাম অয়েল ১০২, মসুর ডাল ৯৬, সয়াবিন ৯৪, গুঁড়া দুধ ৮৪, ময়দা ৮১, আটা ৭৬ এবং গরুর মাংসের দাম ৩৪ শতাংশ বেড়েছে।
তিনি বলেন, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা জরুরি। কারণ, অর্থনীতি টেকসই করতে হলে ব্যাংকিং খাত শক্তিশালী হতে হবে। কিন্তু দিনদিন এ খাত আরও দুর্বল হচ্ছে। ব্যাংকগুলো শক্তিশালী একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করছে। পুরো ব্যাংকিং খাত কিছু ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়েছে। বাড়ছে খেলাপি ঋণের বোঝা। এ খেলাপি ঋণ কমাতে কয়েকটি উদ্যোগ জরুরি। এগুলো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, নিয়ন্ত্রক সংস্থার সংস্কার, আইন সংশোধন এবং তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। তার মতে, সুদের হার কমিয়ে রাখায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর চাপ পড়েছে। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ২০০৮ থেকে ২০২৩ সাল-১৫ বছরে ২৪ প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং খাত থেকে ৯২ হাজার ২৬১ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এ পরিমাণ অর্থ জাতীয় রাজস্ব আয়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশের সমান।
তিনি বলেন, শ্রম অধিকার নিয়ে কথা আসছে। বাংলাদেশের পোশাক খাতের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘ এ নিয়ে কথা বলেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শ্রমিকের অধিকার নিয়ে কয়েকটি বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতা, জোরপূর্বক কাজে বাধ্য করা, শিশুশ্রম বন্ধ করা, কাজের শর্ত গ্রহণযোগ্য হতে হবে, নির্ধারিত শ্রমঘণ্টা এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত বিষয় ও নিরাপত্তা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেশকিছু শর্তের কথা বলেছে। এর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক মান, ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতা, পেশাগত নিরাপত্তা, শিশুশ্রম বন্ধ করা এবং শ্রমিকদের পরিদর্শকদের দক্ষতা বাড়ানো। এছাড়াও জাতিসংঘ কিছু উদ্বেগের কথা বলেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন কনভেনশনে সই করা, দাসত্ব এবং পাচার বন্ধ করা, লিঙ্গবৈষম্য কমানো ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং কাজে যোগদানের জন্য ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ, তাদের শিক্ষা এবং শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।
তিনি বলেন, এসব নিশ্চিত করতে না পারলে আমাদের বাণিজ্য ও রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ২০০৮ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে এটি ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। এছাড়াও ঋণ অবলোপন, বিভিন্ন মামলার জালে আটক থাকা এবং ঋণ পুনর্গঠন হিসাব করলে এটি আরও বাড়বে। তিনি বলেন, বর্তমানে আমাদের বিদেশি ঋণ জিডিপির ২০ শতাংশ। এটি বেশি নয়। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। আমরা যে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করব, সেই রিজার্ভের অবস্থা খারাপ। অন্যদিকে সরকার যে রাজস্ব আয় করছে, সেটি দিয়ে শুধু রাজস্ব ব্যয় মেটানো সম্ভব হচ্ছে। এ খাতে উদ্বৃত্ত থাকছে না। ফলে ঋণ উন্নয়ন প্রকল্প পুরোটাই ঋণের টাকায়। এক্ষেত্রে ঋণ নিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হচ্ছে। এটাকেই আমরা ঋণের ফাঁদ বলছি।







আপনার মূল্যবান মতামত দিন: